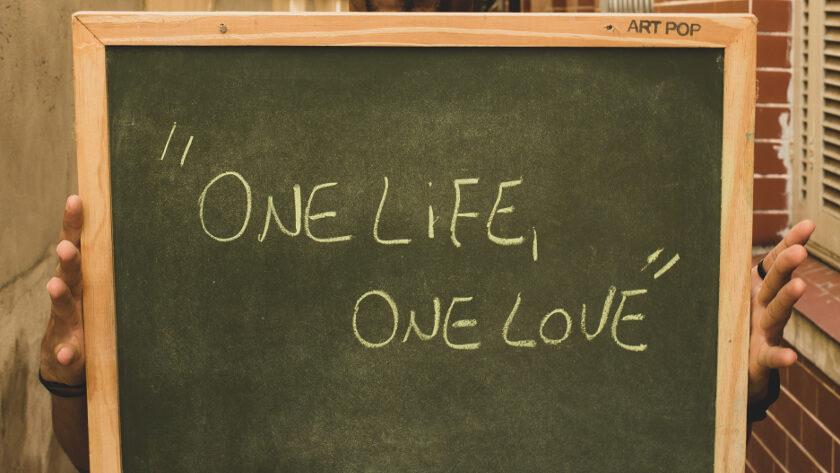A Story Of Inspiration – বেঁচে থাকার গল্প
রোজ তো কত হাবিজাবি লিখি।
আজ বরং একটা সত্য গল্প শোনাই। একজন মেয়ের জীবনে বারবার হেরে যাবার পরেও সুইসাইড না করে শুধুমাত্র নিজেকে প্রবলভাবে ভালোবেসে এবং নিজের স্বপ্নকে ছুঁয়ে দিবে বলেই প্রচন্ডভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়ার গল্পটা বলি।
মেয়েটির জন্ম মা বাবার প্রিন্সেস হিসেবে। শহরের সব থেকে ভালো স্কুল কলেজের একেবারে প্রথম সারির প্রথম ছাত্রী ছিল সে।পুরো স্কুল কলেজ জীবনে সে মাত্র একবার ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হতে পারিনি। বাকী সমস্ত রেজাল্ট কার্ডে এখনো জ্বল জ্বল করে তার ক্রমিক নং— “এক”। পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তিসহ এসএসসিতে স্টার মার্কস ছয় সাতটা লেটারসহ প্রায় নয়শ নম্বর নিয়ে তার ছাত্র জীবনের দৌঁড় শুরু হয়েছিল। ডাক্তার তাকে হতেই হবে— জীবনের একমাত্র লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলার প্রস্তুতির শুরু হয়েছিল পাঁচ বছর বয়স থেকেই !
লেখাপড়াই ছিল তার একমাত্র ধ্যান আরাধ্য। পড়াশোনা করা, নামাজ পড়া, খাওয়া দাওয়া করা আর টুকটাক কালচারাল একটিভি করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার জীবনে। একমাত্র বিনোদন ছিল গল্পের বই পড়া আর দৈনিক পত্রিকাতে লেখা পাঠানো। ব্যাস। এতটুকুই ছিল তার পৃথিবী।
তার স্বপ্ন ছিল—- একদিন বিশাল একজন ডাক্তার হয়ে সে তার নিজের জীবনটা শুরু করবে। তার আগ পর্যন্ত তার জীবনটা সেভাবেই চলবে যেভাবে আব্বু আম্মু চাচ্ছে। বাবা মায়ের প্যাম্পারড চাইল্ড ছিল সে। জীবনে না শব্দ শুনতে হয়নি তাকে সতের আঠার বছর বয়স পর্যন্ত।
তার জীবনটা খুবই গোছানো ফেয়ারি টেইল টাইপ ছিল আরকি।কোন ধরনের কষ্ট সে পায়নি জীবনে মেডিকেল কলেজে এডমিশন দেবার আগ পর্যন্ত।
জীবনে প্রথম ধাক্কাটা সে খায় মেডিকেল কলেজে চান্স না পেয়ে। প্রথমবার বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এডমিশন দেয়নি সে। দ্বিতীয় বারও যখন চান্স হলো না সরকারি মেডিকেলে তখন জীবনে প্রথম বার মরে যেতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু অসাধারণ এক পরিবারের প্রথম সন্তান হবার বদৌলতে সে যাত্রায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এডমিশন দেবার সুযোগ পেল সে। তার বাবা মা একবারও ভাবিনি এত লাখ লাখ টাকা খরচ করে পরিবারের প্রথম সন্তানকে বেসরকারি মেডিকেলে পড়াব? তার ছোট আরো চারজন বোন ছিল। তার বাবা মা বিশ্বাস করতো তাদের মেধাবী মেয়ের ডাক্তার হবার যোগ্যতা অবশ্যই আছে। জীবনে একটা ভর্তি পরীক্ষাতেই তার এত বছরের পরিশ্রম,স্বপ্ন শেষ হয়ে যেতে পারে না।
যদিও মেয়েটি হাজারবার নিজের কাছে নিজে মরে গেছে একথা ভেবে—- যদি কোন কারনে আমার ছোট কোন বোনকে পরবর্তীতে পড়াতে কষ্ট হয় আব্বু আম্মুর? আমি কি পারব নিজে কে ক্ষমা করতে ?
যাহোক আল্লাহর অশেষ রহমতে মেয়েটির পিঠাপিঠি ছোট দু বোন দেশের অন্যতম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই মাস্টার্স শেষ করেছে।আর সব থেকে ছোট দু বোন দেশের বাইরে লেখাপড়া করছে। একজন নিজের লেখাপড়ার খরচ নিজেই জব করে জোগাড় করেছে। আরেকজনেরটা শুরু হলো মাত্র। হয়তো সেও নিজের যোগ্যতাতেই শেষ করে ফেলবে লেখাপড়াটা।
যাহোক মেডিকেলে লেখাপড়া শুরু করলেও মনের দিক থেকে বহু হীনমন্যতায় ভুগতে হতো মেয়েটাকে। আত্মীয় স্বজনের অদ্ভুত সব প্রশ্ন ছিঁড়ে ফেলত তাকে। প্রাইভেট মেডিকেলে পড়ে কি বিসিএস দেয়া যায় ? এফসিপিএস করা যায় ? এসব আজগুবি প্রশ্ন শুনতে শুনতেই দিন কাটতো।
মেডিকেল কলেজে পেইন কম ছিল না। কিছু ব্যাচ টিচার ছিল যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—- নিজের ডিগ্রী না হওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত ফ্রাসট্রেশন ছাত্রদের উপরে ঝাড়ত। স্পেশালী কিছু ফাউন্ডার মেম্বারের সন্তান এবং উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষক হওয়া মহিলা টিচার ছিলেন জাষ্ট ইমপসিবল। আজ এত বছর পরেও মেয়েটির কানে বাজে তাদের A ব্যাচের এনাটমীর abdomen কার্ডের ব্যাচ টিচারের ডায়লগ—— আমার নাহয় শ্বশুরের মেডিকেল কলেজে আছে তাই জব করছি। তোমাদের কি হবে ? তোমরা তো বাবার টাকায় মেডিকেলে পড়ছ।
অথচ বেসরকারি তে লেখাপড়া করলেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট মার্কস থাকতে হতো সে সময়ে এডমিশন টেস্ট দেবার জন্য। তারপর ভর্তি পরীক্ষা হতো। শুধু টাকা জমা দিলেই ভর্তি হওয়া যেত না, এখনো যায় না বেসরকারি মেডিকেল কলেজে।
একজন শিক্ষক কতখানি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলে ঐসব কথা তার ছাত্রদের বলতে পারেন ভাবুন। আমি নিজেও একটা মেডিকেল কলেজে শিক্ষক ছিলাম ছয় মাস। আমার বাবা ঐ মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী।
বাপ চাচা মামার জোর অনেকেরই থাকে। তবে সবাই তা show করে না। কিন্তু ঠিক যেদিন আমি নিজে ফিল করলাম আমি ইনজয় করছি না ছাত্র পড়ানো। অনেক বেশী ধৈর্য দরকার শিক্ষকতা পেশায়। যা আমার নেই। সাথে সাথে আমি রিজাইন করেছি। কিন্তু আজও ঐ মেডিকেলের ছাত্ররা আমাকে মনে রেখেছে।
মেডিকেলে চাপ থাকবেই। ছাত্র শিক্ষক সবাইকেই এ কথা মাথায় রাখা দরকার।
ঐ ম্যাডাম তার ছাত্ররা আইটেম পেন্ডিং করলে দলবেঁধে পুরো ব্যাচকে প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে নিয়ে যেতেন। আমার আইডিতে ঐ ম্যামের ঐ A ব্যাচের প্রচুর ছাত্ররা এড আছে। ওরা সাক্ষী আমি একটা শব্দও মিথ্যে বলছি না। এই ম্যাডাম তার শিক্ষক জীবনের প্রথম ব্যচের এগারো জন ছাত্রের ক্লিয়ারেন্স আটকে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র কিডনি আইটেম পেন্ডিং ছিল বলে। অথচ সত্যটা হচ্ছে ওনার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে তার ছাত্ররা আইটেম পড়ে এসেও লাইব্রেরিতে লুকিয়ে থাকত এনাটমী ক্লাসের সময়ে।
যাহোক, সারা জীবনের ফার্ষ্ট গার্ল মেয়েটি মেডিকেল কলেজের প্রথম প্রফেশনাল একজামিনেশনে বসতেই পারল না !!!! পাশ ফেইল তো পরের কথা। স্যার ম্যামদের বাসা পর্যন্ত দৌঁড়াতে হয়েছিল A ব্যাচের সবাইকে দলবেঁধে। কিন্তু না, হলো না ক্লিয়ারেন্স।
ঐদিন জীবনে দ্বিতীয় বারের মতো মরে যেতে ইচ্ছে হলো মেয়েটির। কিন্তু মরে যাওয়া হলো না। আব্বু আম্মু আর বোনেদের কথা ভেবে মেয়েটি পারল না দুই পাতা সিডেটিভ হাতে নিয়েও খেয়ে ফেলতে।
এরপর মেয়েটির ব্যক্তিগত জীবনে ঝড় তুফান শুরু হলো। ভুল মানুষের সাথে জড়িয়ে জীবনটাকে বায়ান্ন তাস বানানো হয়ে গেল। একদিকে সেকেন্ড প্রফের পাঁচটা সাবজেক্টের লেখাপড়া, হাসপাতালের ওয়ার্ডে দৌঁড়াদৌঁড়ি করে ক্লাস করা , পাশাপাশি non co operative হাজবেন্ড শ্বশুর বাড়ির সহাবস্থান
সব মিলিয়ে হজবরল অবস্থা। সেকেন্ড প্রফের আগে মেয়েটির একবার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হলো। ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকলো কিছুদিন।
কি হবে ডাক্তার হয়ে ? এই মানুষগুলো তো আমাকে চায় না।ওদের দরকার নাতী। ডাক্তার বৌমা ।সে যে কি অসহনীয় অপমান। লিখে বোঝানো সম্ভব না। তখন তৃতীয় বার মনে হলো একটাই সমাধান— মরে যাওয়া।
কিন্তু কেন যেন সার্জারি আর গাইনি পড়তে খুব ভালো লাগতো মেয়েটার। মনে হলো আরো একটু পড়ি সার্জারি । আরো কিছু ওটি দেখি। তারপর নাহয় মরে যাই ! এর মধ্যে সেকেন্ড প্রফ পাশ করে মেয়েটি ফিফথ ইয়ারের চলে এলো। হঠাৎ করেই জানতে পারল সে মা হতে যাচ্ছে। ব্যাস “মরে যেতে চাই” এর মুখে ছাই দিয়ে সারা পৃথিবী কে তুচ্ছ করে শুরু হলো লেখাপড়া। সুস্হ সন্তান জন্ম দেয়া আর ডাক্তার হওয়াই তখন তার জীবন মরণ হয়ে দাঁড়ালো। কে কি বলল কে কি অত্যাচার করল, কতটা ব্যাথা সে পেল শরীরে এবং মনে সব ইগনোর করতেই থাকলো। ইগনোর করতে করতে কখনো যে বাবা মায়ের প্রিন্সেস মেয়েটি পাথর টাইপ হয়ে গেল নিজেও টের পেল না। চোখে জল তখনো সে ফেলতো। দুধের বাচ্চাকে ঢাকাতে মায়ের কাছে রেখে অন্য শহরে ফাইনাল প্রফ দিতে আসা সহজ কাজ ছিল না। প্রেগনেন্সির পরে যে আদর আহ্লাদ সম্মান সব মায়ের প্রাপ্য হওয়া উচিত তা হয়নি মেয়েটির জন্য। নিজেই নিজেকে ভালোবাসতে শুরু করল তখন থেকে। নিজের যত্ন নিতে শুরু করলো। ডাক্তার হতেই হবে। বাচ্চাটাকে নিয়ে সুন্দর জীবন কাটাতেই হবে। কি যে কষ্ট, কি যে কষ্টকর এক একটা রাত ছিল সেই সময়গুলোতে আজও ভাবলে কাঁদতে ইচ্ছে করে চিৎকার করে পাথর সমান শক্ত মেয়েটিরও।
এরপর এলো জীবনের সব থেকে ভয়াবহতম তিনটা বছর। যে তিনটা বছরে অজস্রবার মরে যেতে হয়েছে মেয়েটিকে জীবনের সব থেকে আপন ভাবা মানুষগুলোর আচরন , ব্যবহার আর কথার বানে।
সে কথা লিখলে উপন্যাস হয়ে যাবে। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলি—– ঐ তিনটা ভয়ংকর বছরেও মেয়েটি বসে ছিল না দুঃখবিলাস বিলাস করার জন্য। ‘আমার কি হবে ?/ কেন এমন হলো আমার সাথে?’ এসব ভাবার সময় ছিল না তার।
শুধুই ছুটেছে—– লেখাপড়া, সন্তান, দুইটা তিনটা হাসপাতালে মেডিকেল অফিসারের চাকরি একসাথে নিয়ে,সাথে শারীরিক মানসিক অর্থনৈতিক সামাজিক সব ধরনের অত্যাচার আর অপমানের জ্বালা হজম করে।
কেন যেন মেয়েটি বুঝে ফেলেছিল ডাক্তার হলেই হচ্ছে না, নিজের শক্তি নিজেকেই হতেই হবে —- মানসিক শক্তি আর অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান হলেই তবে মিলবে মুক্তি এই রোজ রোজ মরে যাওয়া জীবন থেকে।
এ সময়েই মেয়েটি পোস্ট গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের জব করা জমানো পয়সা দিয়ে। আজকে পর্যন্ত মেয়েটি একটা দিনের জন্যও বেকার থাকেনি। বাংলাদেশের এমন প্রান্তে গিয়েও সে জব করেছে ছোট্ট সন্তানটাকে বুকে জড়িয়ে যা তার সন্তান বড় হয়ে যখন জানবে সে অবশ্যই গর্ববোধ করবে তার মায়ের সাহসের জন্য। তার মা শুধুমাত্র সম্মানের একটা জীবন সন্তান কে দিবে বলে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়িয়েছে নারী জীবনের রিষ্ক নিয়ে । কারন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ ডেসপারেট হয়ে যায়। হয় মরব নাহয় বাঁচার মতো করেই বাঁচব—– that’s it.
সংসার টেকানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা, যা বাঙালী সব মেয়েই করে তার প্রতিটি স্টেপ মেয়েটি নিয়েছে। কারন মেয়েটি জানতো সুতো ছিঁড়ে গেছে বহু আগেই। তবুও মনের ভেতরে জমে থাকা মায়া মেয়েটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই এক বিন্দু মায়া অবশিষ্ট থাকলেও সে থেকে যাবে , কাটাবে আর সবার মতো ‘ভালো মেয়ের’ একটা অভিনয় সর্বস জীবন।
মেয়েটি লাকি ! খুব বেশি সময় লাগেনি মায়া থেকে বের হয়ে আসতে। জীবনের দশটা বছরের বিনিময়ে মেয়েটি জেনে গিয়েছিল সত্যটা। রোজ অপমান হতে হতে মরে যেতে যেতে ‘ভালোবাসা বড় না অক্ষত হাত পা চোখ নিয়ে বেঁচে থাকা বড় ? ‘
—এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটির চোখে সামনে তার মা,বাবার মুখটা বারবার ভেসে উঠতো। আর বেঁচে থাকার কারন ভাবলেই কোলে খুঁজে পেতে সন্তান কে আর রোগীদের মুখগুলো।
ব্যাস বেঁচে গেল মেয়েটি !
এরপর আর কখনোই মেয়েটির মরে যেতে ইচ্ছে করেনি আজ পর্যন্ত।
আজ মেয়েটি শুধু নিজেই বেঁচে আছে এমন না; আমার মতো আরো অনেক মেয়েকে বেঁচে থাকার গল্প শোনায় সে। চেষ্টা করে আরো অনেক মেয়েকে জীবন নিয়ে সাহসী হবার, স্বপ্ন বিলাসী হবার উৎসাহ দিতে।
এই যে মেয়ে তোকে বলছি ,
ভাগ্যিস তুই মরে যাসনি। তুই মরে গেলে অধরা স্বপগুলো পূরণ হতো না। তোর লেখক হবার দুর্নিবার ইচ্ছাটা হারিয়ে যেত। বেঁচে ছিলি বলেই তো বই লিখে ফেললি। আরো লিখবি জানি।
মরে গেলে তো সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করার নেশা তোর পূরণ হতো না। বৃদ্ধাশ্রমে হেলথ ক্যাম্প কে করত বল্ তো ?
মেয়ে,
তোরা মরে যাস নে এভাবে অবেলাতে প্লিজ।
সৃষ্টিকর্তার উপরে ছেড়ে দে মৃত্যুর সময়টা।
তার আগ পর্যন্ত চল্ বেঁচে থাকি তুই,আমি, আমরা। মাথা উঁচু করে বেঁচে থেকে দেখিয়ে দেই সবাইকে। এমন ভাবে বাঁচি যেন তোর আমার ভালো থাকাটা দেখে আমাদেরকে হারিয়ে ফেলা মানুষগুলো গুমরে মরে, চোখের জলে ভাসে। আর প্রকৃতি যেন তার হিসেব মিলিয়ে দেবার দুষ্টু মিষ্টি খেলাটা খেলতে পেরে মুচকি হাসি হাসে।
.

#মিম্ মি
Photo by David Rangel on Unsplash